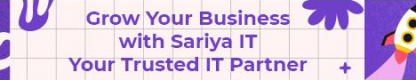ইমতিয়াজ উদ্দিন:
পুরান ঢাকার একটি গলিতে ছড়িয়ে থাকা রক্ত, সিঁড়ির ধাপে লুটিয়ে থাকা তরুণের নিথর দেহ—এই দৃশ্য শুধু একটি খুনের নয়, বরং বিংশ শতাব্দীর ভয়াবহ মানসিক ও নৈতিক সংকটের প্রতিচ্ছবি। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের ছাত্র এবং ছাত্রদল নেতা জুবায়েদ হোসেন খুন হয়েছেন এক ত্রিভুজ প্রেমের নাটকীয় পরিণতিতে, যেখানে প্রেমিকা বর্ষা ও তার দীর্ঘদিনের প্রেমিক মাহীর পরিকল্পিতভাবে তাকে হত্যা করে। এই ঘটনার বিবরণ শুনলে বরগুনার রিফাত শরীফ হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটা মনে পড়ে যায়—সেখানেও প্রেম, প্রতারণা, অধিকারবোধ ও প্রতিশোধের জটিল মিশ্রণ ছিল। প্রেম নামের কোমল আবেগ কীভাবে এক মারণাস্ত্রে পরিণত হতে পারে, তার সবচেয়ে করুণ উদাহরণ এই হত্যাকাণ্ড। কিন্তু প্রশ্ন হলো—এমন ঘটনার পেছনে কী ধরনের মনস্তত্ত্ব কাজ করে? মানুষ কেন ভালোবাসার নামে সহিংসতায় লিপ্ত হয়? কেন প্রেম একসময় সহানুভূতির জায়গা থেকে ঘৃণা ও প্রতিশোধের পর্যায়ে পৌঁছে যায়? এসকল প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে ত্রিভুজ প্রেমের মনস্তত্ত্বের মধ্যে।
ত্রিভুজ প্রেম কোনো নতুন বিষয় নয়। মানুষের আবেগ, আকর্ষণ ও সম্পর্কের জটিলতা যুগে যুগে এমন ভালোবাসার সংঘাত সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আধুনিক সময়ের ত্রিভুজ প্রেমে যে বিপজ্জনক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তা হলো—অধিকারবোধ ও বর্জনের ভয়। মনোবিজ্ঞানের ভাষায়, যখন কোনো ব্যক্তি ভালোবাসাকে “মালিকানা” হিসেবে দেখতে শুরু করে, তখন সেটি আর ভালোবাসা থাকে না—তা হয়ে ওঠে নিয়ন্ত্রণ ও দখলের প্রচেষ্টা। এই মানসিক অবস্থায় যখন প্রেমিক বা প্রেমিকা অন্য কারোর প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন জন্ম নেয় তীব্র হিংসা ও আত্মমর্যাদার সংকট। ডিএমপি’র তথ্য অনুযায়ী, বর্ষা মাহীরকে জানায়—“জুবায়েদকে না সরালে তোমার কাছে ফিরতে পারবো না।” অর্থাৎ, প্রেম এখানে ভালোবাসা নয়, বরং বাধাহীন দখল প্রতিষ্ঠার মনোভাব হয়ে উঠে। এখানেই শুরু হয় মানসিক বিপর্যয়—যেখানে মানবিক বিবেকের জায়গা দখল করে “আমি না পেলে কেউ পাবে না” নামের মানসিক বিকার।
সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে সম্পর্কের গতি দ্রুত, আবেগের গভীরতা অগভীর। একটি ইনবক্স থেকে শুরু হওয়া বন্ধুত্ব কখনো প্রেমে রূপ নেয়, আবার হঠাৎই সেটা সন্দেহ, প্রতারণা ও মনস্তাত্ত্বিক প্রতিযোগিতার জায়গা তৈরি করে। আজকের তরুণ সমাজের একাংশ প্রেমকে পারস্পরিক সম্মান নয়, বরং এক ধরনের “ইগো সন্তুষ্টি” হিসেবে দেখে। যখন সেই সন্তুষ্টি মেলে না, তখন সেই প্রেম রূপ নেয় ঘৃণায়। বর্ষা, মাহির ও জুবায়েদের ঘটনার মধ্যে ঠিক এই বিকৃত প্রেমের রূপটি স্পষ্টভাবে দেখা যায়। মাহীরের নয় বছরের সম্পর্ক ছিল বর্ষার সঙ্গে—এক দীর্ঘ সময়ের আবেগ, প্রত্যাশা ও বিশ্বাসের বিনিময়। কিন্তু বর্ষার হঠাৎ জুবায়েদের প্রতি আকর্ষণ তৈরি হলে মাহীরের মস্তিষ্কে জন্ম নেয় অধিকার হারানোর আতঙ্ক। সেই আতঙ্ক থেকেই জন্ম নেয় প্রতিশোধের গভীর তৃষ্ণা যা মাহীরকে প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তোলে। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, “Rejection” বা “প্রত্যাখ্যান” মানুষের মস্তিষ্কে শারীরিক ব্যথার মতোই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই ব্যথা যদি অনিয়ন্ত্রিত থাকে, তা অনেক সময় ঘৃণা ও সহিংসতার জন্ম দিতে পারে।
প্রেমের এমন বিপর্যয় একদিনে তৈরি হয় না। এর পেছনে কাজ করে পরিবার ও সমাজের নীরবতা। আমাদের পরিবারে এখনও “প্রেম” শব্দটি অনেক ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ বিষয়। তরুণরা প্রেমে পড়লে বা সম্পর্কের সংকটে পড়লে তারা কাউকে কিছু বলতে পারে না। পরিবার বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মানসিক শিক্ষা, আবেগ নিয়ন্ত্রণ, সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা নিয়ে কোনো আলোচনা হয় না। ফলে সম্পর্কের ভাঙন বা প্রত্যাখ্যানের মুখে তারা একা হয়ে পড়ে—যেখানে চিন্তা বিকৃত হয়, সিদ্ধান্ত অন্ধ হয়ে যায়। জুবায়েদের হত্যার ঘটনা তেমনই এক মনস্তাত্ত্বিক নিঃসঙ্গতার প্রতিচ্ছবি। যেখানে শেখানো হয়নি ভালোবাসার সংজ্ঞা, শেখানো হয়নি ভালোবাসার সীমা ও দায়িত্বও।
বাংলাদেশসহ উপমহাদেশে চলচ্চিত্র, নাটক, ওয়েব সিরিজে প্রায়শই দেখা যায়—প্রেমে ব্যর্থ নায়ক প্রতিশোধ নেয় অথবা প্রেমিকার জন্য প্রাণ দেয়। এই রোমান্টিক সহিংসতার সংস্কৃতি তরুণদের মনে এক ধরনের “Hero Complex” বা “হিরো জটিলতা” তৈরি করে—যেখানে তারা মনে করে, ভালোবাসা প্রমাণের একমাত্র উপায় হলো চূড়ান্ত ত্যাগ বা সহিংসতা। জুবায়েদ হত্যায় মাহীরের ভূমিকা ছিল এমনই এক হিরো ভাবনার প্রতিফলন। বর্ষাকে কাছে ফিরে পাওয়ার জন্য মাহীর শুধু প্রেমিক নয়, বরং এক সহিংস যোদ্ধা হয়ে উঠেছিল। এই বিকৃত রোমান্টিক ধারণাই তাকে ঠেলে দিয়েছে অপরাধের সীমানায়। সোশ্যাল মিডিয়াও এখন আবেগ উস্কে দেয়—সেখানে প্রেম, প্রতারণা, ব্রেকআপ ও প্রতিশোধকে “ট্রেন্ড” হিসেবে দেখা হয়। যুব সমাজের একাংশ এই নাটকীয় উপস্থাপনাকেই বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে শুরু করে।
প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বর্ষার সঙ্গে মাহীরের সম্পর্ক ছিল নয় বছরের। তাদের আবেগের ভিত্তি ছিল দীর্ঘ সময়ের ভালোবাসা, কিন্তু এর মধ্যে প্রবেশ করে জুবায়েদ—এক তরুণ শিক্ষক, যিনি বর্ষাকে প্রাইভেট পড়াতেন। এখানে তৈরি হয় এক নতুন মানসিক সমীকরণ—বর্ষার মনে নতুন আকর্ষণ, মাহীরের মনে পুরনো অধিকারবোধ আর জুবায়েদের মনে নিষ্পাপ বিশ্বাস। এই তিনটি আবেগের সংঘর্ষই তৈরি করে ত্রিভুজ প্রেমের ট্র্যাজেডি। মনোবিজ্ঞানের “Jealousy Theory” বা “হিংসা তত্ত্ব” অনুযায়ী, প্রেমে হিংসা তখনই জন্ম নেয় যখন ব্যক্তি তার আত্মমর্যাদার সঙ্গে প্রেমিকাকে সমান করে দেখে। বর্ষার প্রত্যাখ্যান মাহীরের কাছে প্রেম হারানো নয়, বরং নিজের অস্তিত্বের উপর আঘাত। ফলে বর্ষার এক কথায়—“জুবায়েদ না মরলে আমি মাহীরের হবো না”—সে নিজের নৈতিকতা হারিয়ে ফেলে। ঘটনার সবচেয়ে করুণ অংশ হলো, জুবায়েদ মৃত্যুর আগে বর্ষার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, “আমাকে বাঁচাও।” কিন্তু বর্ষা উত্তর দিয়েছিল—“তুমি না মরলে আমি মাহীরের হবো না।” এই এক সংলাপেই ফুটে ওঠে আধুনিক প্রেমের বিকৃত চেহারা—যেখানে ভালোবাসা নয়, অধিকার ও প্রতিযোগিতাই যেন মূল বিষয়।
ত্রিভুজ প্রেমের এই ঘটনাগুলোকে যদি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়, তবে প্রথমেই আসে মানবিক নিয়ন্ত্রণ ও নৈতিকতার প্রশ্ন। ইসলাম, খ্রিস্টান, সনাতন—প্রতিটি ধর্মই মানুষের ভালোবাসাকে স্বীকৃতি দিয়েছে, কিন্তু ভালোবাসার সঙ্গে দায়িত্ব, সম্মান ও সীমারেখা রক্ষা করাকেও করেছে বাধ্যতামূলক। ইসলামে প্রেম বা ভালোবাসা কখনো নিষিদ্ধ নয়; বরং তা নিয়ন্ত্রিত ও পবিত্র রূপেই অনুমোদিত। কুরআন-হাদিসের বিভিন্ন জায়গায় প্রেম স্থাপনের জন্য বিবাহ করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে—অর্থাৎ প্রেমের লক্ষ্য হওয়া উচিত দায়িত্বপূর্ণ সম্পর্ক, কেবল আবেগের তাড়না নয়। কিন্তু ত্রিভুজ প্রেমে সাধারণত দেখা যায়, একাধিক মানুষের প্রতি একসঙ্গে আকর্ষণ যা প্রতারণার প্রবণতা তৈরি করে। এটা ইসলামী শরিয়াহর দৃষ্টিতে গুরুতর নৈতিক অপরাধ। এটি জিনার মতো (অবৈধ সম্পর্ক) এক মানসিক প্রবণতা, যা সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করে।
খ্রিস্টান ধর্মেও প্রেমকে ঈশ্বরপ্রদত্ত এক পবিত্র অনুভূতি হিসেবে দেখা হয়। বাইবেলে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, “তুমি ব্যভিচার করবে না।” অর্থাৎ, প্রতিশ্রুত সম্পর্কের (বিবাহ) বাইরে অন্য কারোর প্রতি আকর্ষণকে পাপ হিসেবে গণ্য করা হয়। এখানেও ত্রিভুজ প্রেমকে দেখা হয় আত্মিক দুর্বলতা ও নৈতিক ভ্রান্তির প্রতীক হিসেবে। কারণ এতে শুধু একজনের নয়, তিনজনের মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক শান্তি নষ্ট হয়।
হিন্দু ধর্মেও প্রেম ও সম্পর্ককে ধর্ম (ধর্মাচরণ)-এর অংশ হিসেবে দেখা হয়। কামকে জীবনের এক পর্ব বলা হলেও তা ধর্ম ও অর্থ এর সীমায় বাঁধা। মনুষ্যজীবনের চার পুরুষার্থ—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। এর মধ্যে কামকে সবচেয়ে নিয়ন্ত্রিতভাবে উপভোগ করার কথা বলা হয়েছে। গীতা ও উপনিষদে বারবার বলা হয়েছে যে, ইন্দ্রিয়ের আসক্তি মানুষকে মোহে ফেলে এবং মোহ থেকেই জন্ম নেয় ক্রোধ ও বিনাশ। ত্রিভুজ প্রেমের ভেতরেও সেই মোহ, ঈর্ষা, ক্রোধ, এবং পরিণামে ধ্বংসের এই চক্রটি স্পষ্টভাবে কাজ করে।
সব ধর্মই মূলত এক কথা বলে—প্রেম মানে আত্মত্যাগ, দায়িত্ব, ও আত্মনিয়ন্ত্রণ। কিন্তু আধুনিক সমাজে যখন প্রেম কেবল আবেগ, আকর্ষণ, ও দখলবোধে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন তা ধর্মীয় ও নৈতিক কাঠামো ভেঙে দেয়। এই কারণেই ত্রিভুজ প্রেম কেবল সামাজিক নয়, এক গভীর আধ্যাত্মিক সংকটও বটে—যেখানে মানুষ নিজের আত্মাকে ভুলে গিয়ে অন্যের প্রতি মালিকানা দাবি করতে শুরু করে। ধর্মীয় বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে, ত্রিভুজ প্রেম হচ্ছে সেই অবস্থার প্রতিফলন যেখানে ভালোবাসা তার পবিত্রতা হারিয়ে লালসা, প্রতিযোগিতা ও প্রতিশোধে রূপ নেয়। তাই ধর্মীয়ভাবে এই ধরনের সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ, আত্মশুদ্ধি ও দায়িত্ববোধের মাধ্যমে রূপান্তর করা প্রয়োজন যাতে ভালোবাসা সত্যিকার অর্থে ফিতনা না হয়ে বরং রহমত হয়ে থাকে।
এবার জুবায়েদের হত্যাকাণ্ডে ফিরে আসা যাক। এরূপ ত্রিভুজ প্রেমঘটিত হত্যাকাণ্ড সমাজের জন্য এক বড় সতর্ক সংকেত। এটি কেবল একটি অপরাধ নয়, বরং একটি প্রজন্মের মানসিক বিপর্যয়ের প্রতিচ্ছবি। আমাদের স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনোই শেখানো হয় না—কীভাবে আবেগ সামলাতে হয়, প্রত্যাখ্যান মেনে নিতে হয়, সম্পর্ক ভাঙলেও সম্মান বজায় রাখতে হয়। তরুণদের আবেগকে “বয়সের ভুল” বলে এড়িয়ে যাওয়াই পরিবার ও সমাজের সবচেয়ে বড় ভুল। প্রেম, সম্পর্ক, ব্রেকআপ, মনস্তাত্ত্বিক স্থিতি—এসব বিষয়ে কাউন্সেলিং সেন্টার ও সচেতনতা প্রোগ্রাম থাকা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক ক্লিনিক বা সেশন বাধ্যতামূলক করা উচিৎ। এছাড়া মিডিয়ায় সহিংস প্রেমকাহিনি প্রচারের পরিবর্তে সহানুভূতি, আত্মসংযম ও আত্মসম্মান শেখানোর বার্তা থাকা দরকার।
রিফাত শরীফ, জুবায়েদ হোসেন—এরা কেউ কেবল নাম নয়, বরং এরা ত্রিভুজ প্রেমের নির্মম শিকারের নমুনা সমাজের, যেখানে ভালোবাসা হারিয়েছে মানবিকতা, যেখানে হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে সম্পর্কের সমাপ্তি হয়েছে আর যেখানে প্রেমের স্থানে এসেছে অহংকারের রাজত্ব। আমরা এমন এক প্রজন্ম গড়ে তুলছি যারা ভালোবাসা মেনে নিতে পারে, কিন্তু ভালোবাসা হারানো মেনে নিতে পারে না। যারা পেতে জানে, কিন্তু ছাড়তে জানে না। এ কারণেই প্রেমের পরিণতি এখন কবিতা নয়, হয়ে উঠছে হত্যাকাণ্ডের শিরোনাম। শেষ প্রশ্ন একটাই—জুবায়েদের দেহে যে ছুরি ঢুকেছিল, তা কি সত্যিই মাহীরের হাতে ছিল, নাকি সেই ছুরির ধার আমরা সবাই মিলে তৈরি করেছি আমাদের নীরব সমাজ, বিকৃত প্রেমচর্চা আর মানসিক ও ধর্মীয় শিক্ষাহীনতার মাধ্যমে?
লেখক:
শিক্ষার্থী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়